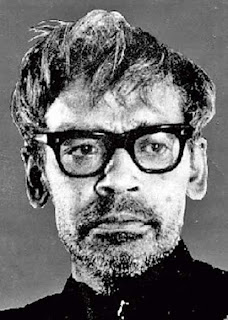চিওপ্রিয় ঘোষ তখনও শঙ্খ ঘোষ হয়ে ওঠেন নি। সেটা ১৯৫২ সাল। খাদ্যের দাবি তে আন্দোলন নিয়ে রাস্তায় সাধারণ মানুষের মিছিলে পুলিশের গুলি ও এক বিয়ে - ঠিক - হয়ে - যাওয়া তরুণীর মৃত্যু (সম্ভবত চার জন মারা গিয়েছিলেন) ও তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তরুণ চিত্তপ্রিয়কে রোমান্টিক অবসেসন্ থেকে বাস্তবের রুক্ষতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। তাঁর উদ্ধত কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাংলা কবিতার এক অনবদ্য কালজয়ী সৃষ্টি -
My blog dates back to 2008. My discomfort with keyboard typing and laziness too prevented me from updating this blog regularly. I penned my feelings, my thoughts, my memories mostly on paper whenever I could manage time. I lost a good number of my writings thanks to my disorganised nature. Let the remaining writings, scattered over here and there, find their destination here in my web space. And let me promise that I will go on updating this blog with my future writings, if that happens!
Monday, April 22, 2024
শঙ্খ ঘোষ
Monday, April 8, 2024
ঋত্বিক ঘটক
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২৬/০৯/২০২৩
Friday, April 5, 2024
পূর্ণেন্দু পত্রী
"পুরনো পকেট থেকে উঠে এল
Wednesday, June 23, 2021
নবারুণ ভট্টাচার্য
হৃদয়ই যখন রাষ্ট্র, ভালবাসা সন্ত্রাসজনিত।পুড়ে গেছে দেশ, তবু চেতনায় ধরেনি আগুন...কে আর বিশ্বাস করবে, আমাদেরও ছিল নবারুণ?"
সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন যে বাঙালিদের একজন নবারুণ ছিলেন! প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ও নবারুণ ভট্টাচার্য সমার্থক হয়ে গেছিল। ১৯৪৮ সালের আজকের দিনেই মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে ঔপনাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, কবি ও চিরবিদ্রোহী নবারুণ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মানবাধিকার কর্মী মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান ছিলেন নবারুণ ভট্টাচার্য। সাহিত্য ও শিল্পচর্চা উত্তরাধিকার সূত্রেই মজ্জাগত। দাদু ছিলেন কল্লোল যুগের নামকরা লেখক মণীষ ঘটক ও ছোটদাদু ছিলেন প্রতিভাবান চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক।
প্রথমে ভূতত্ববিদ্যা (আশুতোষ কলেজ) ও পরে ইংরেজি সাহিত্য (সিটি কলেজ) নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেন। কলেজের পড়া শেষ করে উনি "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন এবং দীর্ঘদিন ওই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে কর্মজীবন বলতে তাঁর আজীবন সাহিত্য সাধনার কথাই মূলতঃ বোঝায়। ১৯৬৮ সালে প্রথম ছোটগল্প 'ভাসান' লিখেই তাঁর লেখক সত্ত্বার আত্মপ্রকাশ। গল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি কবিতাও লিখতেন নিয়মিত। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়"। বাহাত্তরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ দিয়ে শুরু হয় তাঁর কবিতার পথ চলা। প্রান্তিক মানুষদের অসহায়, যন্ত্রণাক্লিষ্ট যাপনচিত্র, তাদের টিকে থাকার লড়াই ও বেঁচে থাকার কৌশল বারেবারে ঘুরে ফিরে এসেছে ওঁনার কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ন নতুন একটি স্বকীয় ধারার সৃষ্টি করেন উনি। মানুষের দুঃখ দুর্দশা, পরাজয় এবং পরিণামে মৃত্যু ও আত্মহননের আলেখ্য তাঁর গল্প, উপন্যাস ও কবিতা জুড়ে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হারবার্ট'। সত্তরের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাস আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলো। এই উপন্যাসের জন্যই ১৯৯৪ সালে নরসিংহ দাস পুরস্কার, ১৯৯৬ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও ১৯৯৭ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন নবারুণ ভট্টাচার্য।পরবর্তীকালে এই উপন্যাসকেই একই নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন পরিচালক ও নাট্যকার সুমন মুখোপাধ্যায়। ৫৩ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে 'হারবার্ট' শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়। ওঁনার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলি হল 'কাঙাল মালসাট', 'লুব্ধক', 'মসোলিয়ম', 'খেলনানগর', 'হালাল ঝান্ডা', 'রাতের সার্কাস' ইত্যাদি। প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যেই ওঁনার প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভাবমূর্তি ধরা পড়ে। তাঁর লেখা 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসটিকে সুমন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ও পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।
তিনি ফ্যাতাড়ু নামে একটি জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র তৈরী করেন এবং ততোধিক জনপ্রিয় শব্দবন্ধ 'ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই' তাঁরই লেখনীর ফসল। এই ফ্যাতাড়ুরা আসলে হতভাগ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি। সাহিত্যের চিরাচরিত নিয়ম ভাঙায় সিদ্ধহস্ত নবারুণ বাবুর ফ্যাতাড়ুরা ছিল ভাষা ব্যবহারে সাহসী ও আচরণে নির্ভীক। এই ফ্যাতাড়ুরা এতই জনপ্রিয় ছিল যে একটা সময় দেখেছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তরুণীদের টি-শার্টের সামনে পিছনে 'ফ্যাতাড়ু' এবং 'ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই' লেখা থাকতো!নবারুণ বাবু কোনোদিনই নামী সংবাদপত্র বা জার্নালের জন্য লেখেন নি। লেখালেখির পাশাপাশি উনি মঞ্চে অভিনয়ও করেছিলেন এবং অভিনয়ই ওঁনাকে ধীরে ধীরে পরিচিতি দেয়। আজীবন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী থাকলেও কখনোই কোনো সরকারের তাঁবেদারি করেন নি বা কোনো সরকারের কাছাকাছি ঘেঁসেন নি। নিজেকে একজন প্রান্তিক মানুষ বলে পরিচয় দিতেন ও জীবনযাপন ছিল প্রকৃত অর্থে অনাড়ম্বর। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের আরামপ্রিয় জীবনের অভিলাষ ও তাদের অনুভূতিহীনতা নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার জন্য হয়তো শিল্প সাহিত্যের প্রশাসক মহলে উনি কিছুটা হলেও ব্রাত্য ছিলেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে অনেকে ওঁনাকে নিয়ে অস্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন।
২০১৪ সালের ৩১শে জুলাই অগ্নাশ্যয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে উনি প্রয়াত হন। কলকাতার কেওড়াতলা মহাশশ্মানে যখন ওঁনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে, তখন সেই শহরেই মঞ্চস্থ হচ্ছে ওঁনারই অনুবাদ করা নাটক 'যারা আগুন লাগায়'! নাটকীয় সমাপতন!জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই নবারুণ ভট্টাচার্য।
সুমন সিনহা ২৩/০৬/২০২১Monday, April 19, 2021
উৎপল দত্ত
১৯২৯ সালের আজকের দিনেই অবিভক্ত বাংলার বরিশালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা ও পরিচালক এবং আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের অবিসংবাদী ব্যাক্তিত্ব উৎপল রঞ্জন দত্ত ওরফে উৎপল দত্ত ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। আমৃত্যু গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী হিসেবেই নিজেকে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে সর্বদা মঞ্চ কে ব্যবহার করে এসেছেন। কখনো রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা আদর্শের সাথে আপোষ করার প্রয়োজন পড়েনি। তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মঞ্চের কারিগর। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, খলনায়কের ভূমিকায়ও সমান দক্ষতায় অভিনয় করে গেছেন। মননশীল সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি অজস্র বানিজ্যিক বাংলা ও হিন্দি ছবি তে সমান পারদর্শিতায় অভিনয় করেছেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় পুরষ্কার ছাড়াও একাধিক জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সাফল্যের চূড়ায় থেকেও ওঁনার পা সবসময় মাটিতেই থেকেছে। দিনের শেষে নিজেকে নাট্য আন্দোলনের একজন কর্মী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের একজন চর্চাকারী হিসেবেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। নির্ভীক চিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ ও নিজস্ব প্রতিবাদের ধরণের জন্য উৎপল দত্ত এক ব্যতিক্রমী ব্যাক্তিত্ব হিসেবেই ইতিহাসে পরিগণিত হবেন। জন্মবার্ষিকী তে এই ক্ষণজন্মা বাঙালি কে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।
১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায় মারা যাওয়ার পর ভারত সরকারের National School of Drama ও Sahityo Akademi এর আমন্ত্রণে উৎপল দত্ত যে বক্তৃতা টি দিয়েছিলেন, সেখান থেকেই ওঁনার মেধা, মনন, নিজস্বতা (originality) ও জ্ঞানের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। নিচে সেই বক্তৃতার লিঙ্ক টি দিলাম। সময় পেলে ও সম্ভব হলে শুনবেন।
সুমন সিনহা২৯/০৩/২০২১Click to listen: Utpal Dutt's speech on Satyajit Ray
সমরেশ মজুমদার
'দৌড়' দিয়ে শুরু করেছিলেন। তারপর একের পর এক। উত্তর আধুনিক বাঙালি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যাপনের আয়না ওঁনার সৃষ্টি। সাবলীল লেখনীর কোথাও কোনো ভণিতা নেই। কখনো কোনো ছদ্মনাম ব্যবহার করেন নি। সব ধরণের সামাজিক স্তর থেকে উঠে এসেছে ওঁনার গল্প ও উপন্যাসের চরিত্ররা। সমস্ত রচনাই উপলব্ধির, বিশ্বাসের, নির্মাণের। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কখনো বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন নি। বাস্তববিচ্যুত না হয়েই উনি যেমন স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তেমনই নিখুঁত ও দক্ষ হাতে সময়ের ছবি কে ধরে রেখেছেন। 'গর্ভধারিণী' তে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে উঠে আসা সুদীপ, আনন্দ, কল্যাণ ও জয়িতা যেমন সমবেতভাবে এক সংস্কারমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখে, তেমনই নিজের রাজনৈতিক বোধ কে লুকিয়ে না রেখে এক অশান্ত সময়ের জ্বলন্ত দলিল লিখে যান 'কালবেলা' তে। সাহিত্যের ইতিহাসে জন্ম দেন কালজয়ী চরিত্র মাধবীলতা কে। আভিধানিক অর্থে যে অবলম্বন ছাড়া বেড়ে উঠতে পারেন না, বাস্তবের মাটি তে সে ই 'আলোকস্তম্ভের মতো একা'। যার সোচ্চার দাবি শুধু 'খরতপ্ত মধ্যাহ্নে এক গ্লাস শীতল জল' হতে চাওয়া। অসীম সম্ভাবনাময় একটা সামাজিক বিপ্লবের ব্যর্থতায় ও স্বপ্নভঙ্গের গ্লানি ও বেদনায় জর্জরিত, আচ্ছন্ন, শ্রান্ত ও ক্লান্ত অনিমেষরা পঙ্গু ও হতাশ অবস্থায় যখন আবিষ্কার করে 'বিপ্লবের অপর নাম মাধবীলতা', তখন জীবনের সত্যই জয়লাভ করে। ভুল বুঝতে পারার থেকে মূল্যবান আর কি হতে পারে!!
জন্মদিনে শ্রদ্ধা ও প্রণাম সমরেশ মজুমদার মহাশয়। ভালো থাকবেন। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।সুমন সিনহা১০/০৩/২০২১
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য
'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।'দু' বোতল মহুয়া পান করার পর যাঁর কলম থেকে এই অসামান্য সৃষ্টি বেরিয়ে আসে, তাঁকে নিশ্চিন্তে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কবি আখ্যায়িত করলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। মধ্যরাতে যে রাগী যুবক কলকাতা শাসন করতেন, নভেম্বর ইশতেহার (১৯৬১) প্রকাশ করে হাংরি আন্দোলনের জনকও তিনি। সাহিত্যিক মতান্তরের জন্য অনায়াসে যিনি আবার ১৯৬৩ সালে হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন। জীবনের প্রতি উদাসীনতা সম্ভবত ওঁনার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল।! ১৯৫৮ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকের কাছে জমা দেওয়ার পর তা যখন প্রকাশ পায় তখন ১৯৬১! তাঁর আদরের 'নিকষিত হেম' ততদিনে 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য' হয়ে গেছে!! একমাত্র কবিতার কাছেই শুধু দায়বদ্ধতা থাকলে বোধহয় এরকম করা যায়।উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাউন্ডুলেপনা ওঁনার জীবনের সাথে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই কোনদিন শৃঙ্খলে বন্দী থাকেন নি। হয়তো সেটাই ওঁনার রুটিন ছিল! তবুও 'অভিমানী প্রেমিকার মত ' লিখেছেন 'চন্দনের ধূপ আমি কবে পুড়িয়েছি মনে নেই, মন আর স্মৃতিগুলি ধরে না আদরে।' বাউন্ডুলে অনেকদিন আগেই ঘুমিয়েছেন। তবুও প্রশ্নগুলো থেকেই যায় যে কে বেশি পাগল, কবি না কবিতা... কে বেশি মাতাল, কবি না কবিতা... যদিও পদ্য বা মহুয়া, কারোরই দায় নেই সেই হিসেব দেওয়ার। কবি না কবিতা, কে বেশি ক্লান্ত সেই তর্কে না গিয়ে এই প্যান্ডেমিক ক্লান্তিতেও কানে বাজে তাঁরই কবিতার লাইন... 'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া'২৫/১১/২০২০শুধু 'রাতের কড়া নাড়ার' বদলে মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্সের হৃদয়বিদারক আওয়াজ শুনতে পাই। যুঝবার 'শক্তি' দিও। জন্মদিনে প্রণাম ও শ্রদ্ধা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।সুমন সিনহা২৫/১১/২০২০
ঋতুপর্ণ ঘোষ
সেদিনের পর থেকে কতো সিনেমার "শুভ মহরৎ" হলো, কতো "বাড়িওয়ালি" সিনেমার শুটিং-এর জন্য তাদের বাড়ি ভাড়া দিলেন, কিন্তু সিনে...

-
School educators, parents, academic professionals and my friends in social network, my elder sister Sutapa Sinha (whom I dearly call as didi...
-
" ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ব্যারিকেড করো প্রেমের পদ্যটাই বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকেই চাই।" ভ্যালেন্টাইনস দিবসের উৎস নিয়ে ন...
-
কোনো কোনো দিন বড় স্মৃতিমেদুর করে তোলে। আজ সরস্বতী পুজো। ভালোবাসার বসন্ত পঞ্চমী। আজকের দিনটি আমায় অতীতচারী করে তোলে। মফস্বল শহরের সরস্বতী পু...